ছবিঃ প্রতীকী
ভাঙা সিংহদুয়ারের ধ্বংসস্তূপের সামনে দাঁড়ালে আজও যেন ভেসে আসে ঢাকের শব্দ। শিউলি ফুলের গন্ধে ভরে ওঠা বাতাসে তখনও মিশে থাকে ধূপের ধোঁয়া, দূরে কোথাও বাজে সানাই। কালের ভারে ক্ষয়ে যাওয়া প্রাসাদের দেয়ালগুলো যেন ফিসফিস করে বলে যায় অতীতের গল্প। ঊনবিংশ শতক। প্রজাদের চোখে এই জমিদার বাড়ি ছিল বাঁচার ভরসা, আবার মহাধুমধামে হয়ে চলা দুর্গা পুজোর কেন্দ্রও। অযোধ্যার দেবোত্তর এস্টেট আজও বাঁচিয়ে রেখেছে সেই প্রায় ২০০ বছরের ইতিহাস।
ঊনবিংশ শতকের গোড়ায় শুরু হয়েছিল এই কাহিনির। রামমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, যিনি প্রথমে শ্রীরামপুরে নীলকর চিক সাহেবের সাধারণ কর্মচারী ছিলেন, নিজের কর্মদক্ষতা ও বিশ্বস্ততায় তাঁর প্রিয়পাত্র হয়ে ওঠেন। চিক সাহেবের মৃত্যুর পর তাঁর উইল অনুযায়ী ইজারা নেওয়া জমির অর্ধেক ভাগ রামমোহনের হাতে আসে। সেই সম্পত্তির জোরেই অযোধ্যায় জমিদারির সূচনা হয়, যা ক্রমে বাঁকুড়া, হুগলি ছাড়িয়ে সুদূর বেনারস পর্যন্তও বিস্তৃত হয়েছিল।
এই জমিদারি ছিল অন্যরকম। নীলকর সাহেবদের মতো প্রজাদের উপর অত্যাচার নয়, বরং চাষবাসের স্বাধীনতাই ফিরিয়ে দিয়েছিলেন জমিদার। এতে ব্রিটিশদের সঙ্গে দূরত্ব বাড়লেও জমিদারি থেকে প্রাপ্ত আয়েই গড়ে ওঠে বিশাল দেবোত্তর এস্টেট। সেখানে নির্মিত হয় দ্বাদশ শিবমন্দির, রাসমঞ্চ, গিরি গোবর্ধন মন্দির, দোলমন্দির ও ঝুলনমন্দির। পারিবারিক বিভেদের ফলে এস্টেটেই পৃথকভাবে দুর্গাপুজোর সূচনা হয়। স্বাধীনতার পর জমিদারি প্রথা বিলোপ হলেও এই দুর্গোৎসব আজও মহাধুমধামে পালিত হয়ে চলেছে।
সময়ের আঘাতে ভেঙে পড়েছে সিংহদুয়ার, নহবতখানা, খাজাঞ্চিখানা, লেঠেল ব্যারাক। তবুও দেবোত্তর এস্টেটের মন্দিরগুলো আজও প্রমাণ করে গৌরবের ইতিহাস। পুজো এলে দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে থাকা পরিবারের সদস্যরা ফিরে আসেন পৈতৃক ভিটেয়। রুপোর পালকিতে কলা বৌ প্রবেশ করেন মন্দিরে, বাজে ঢাক-সানাই, ব্যবহার হয় রুপোর বাসনপত্র। পরিবারের সদস্যরা বলেন, সময়ের সাথে জৌলুস কমলেও আবেগে একটুও ভাঁটা নেই। ঐতিহ্যের টানে আশপাশের মানুষও আজও ভিড় জমান অযোধ্যার এই পুজোয়।



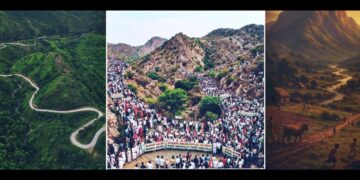










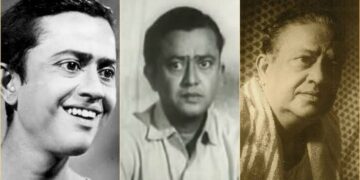




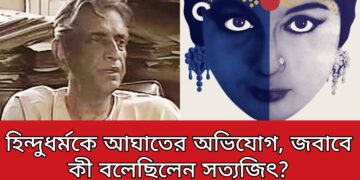
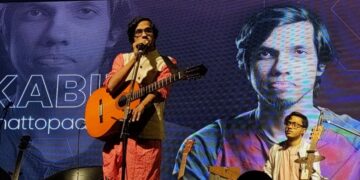



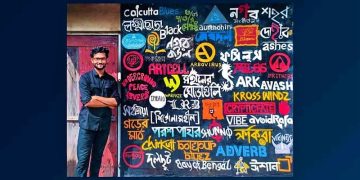






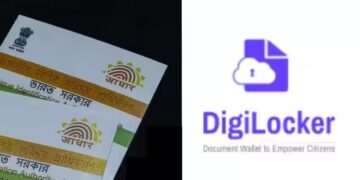










Discussion about this post