“শীতের হাওয়ায় লাগলে নাচন আমলকীর ওই ডালে ডালে।” শীতের হাওয়া কি শুধুই আমলকি বনের বুক দুরুদুরু কাঁপাচ্ছে নাকি? না, একেবারেই তা নয়। সোয়টার, মাফলার ঢেকেই আগুনের সামনে বসেছে মানুষ তাপ নিতে। ওদিকে আবার শীতে উৎসবেরও ডালি ভরা। ক্রিসমাসের জিঙ্গল বেল সুর বেজে উঠল বলে। বিদেশীদের সঙ্গে হেঁটে এলেও ক্রিসমাস এখন গোটা ভারতের উৎসব। আর এতে বাংলার উৎসাহ সবচাইতে বেশী। কারণ বাংলার অঢেল সম্পদের আকর্ষণে, একের পর এক বিদেশীর আগমন ঘটেছিল বাংলাতেই। ফলে রয়ে যায় তাদের স্মৃতিসুলভ উপাসনালয়গুলো। বাংলার দিকে দিকে চার্চগুলো আজও সেজে ওঠে বড়দিনের আনন্দে। কিন্তু তার বেশিরভাগই আমাদের চোখ এড়িয়ে গেছে। চলুন আজ তেমনই স্বল্প পরিচিত এক চার্চের অতীত জেনে দেখি। যার নাম মুরগিহাটার গীর্জা।
ষোড়শ শতকের শেষ থেকে সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগ। বাণিজ্যের আশায় বাংলায় পর্তুগীজরা ঘাঁটি গড়ে চলেছে। বাংলার মূলত পশ্চিম অংশে এরা বসতি স্থাপন করেছিল। জব চার্নক তখন মুঘলদের সঙ্গে বিরোধ করেন বাংলার সুতানটিতে আসেন। বাংলায় তখন পর্তুগীজ আধিপত্য। তাদের সহায়তাতেই জব চার্নক বাস শুরু করেন এখানে৷ খড়ের চালা দেওয়া একটা অস্থায়ী উপাসনাগারও তৈরি করেছিল তারা৷ কলকাতার আদি খ্রিস্ট উপাসনালয়৷ অনেকের মতে, ১৬৯৩-এ চার্নকের মৃত্যুর পর সুতানটি থেকে কুঠি তুলে দেওয়া হয়। পর্তুগীজদের কুঠি থেকে বিতাড়িত করে তাদের জায়গা দখল করা হয়৷ তৈরী হয় নতুন ইংরেজ কুঠি। বর্তমানের ডালহৌসির জিপিও এলাকা।

বিতাড়িত পর্তুগিজরা খানিকটা দূরে এখনকার মুরগিহাটা অঞ্চলে চলে আসে৷ এখানে আরও একটি উপাসনালয় তৈরী করে। সেটি ছিল অস্থায়ী কাঠামো৷ পরে ১৭৯৭-তে নতুন গির্জাভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়৷ গির্জা তৈরীতে খরচ হয় নব্বই হাজার সিক্কা টাকা৷ পর্তুগিজ ধনী ব্যবসায়ী অনেক টাকা দান করেন ওই গির্জার জন্যে৷ নির্মাণকাজ সম্পূর্ণ হলে ১৭৯৯ সালের ২৭ নভেম্বর চার্চ খুলে দেওয়া হয়৷ দু’দিকে দু’টি মিনার, মাঝে ত্রিভুজাকৃতি চুড়োর গঠন, কলকাতার অন্যতম সুন্দর-দর্শন।
কলকাতার অন্যতম সুন্দর-দর্শন চার্চটি।ব্রেবোর্ন রোডে অবস্থিত। পর্তুগিজ এই চার্চে পা রাখলেই মনে নেমে আসে এক প্রগাঢ় শান্তি। বড়দিনের আগে থেকে শুরু হয় সাজো সাজো রব। পর্তুগিজদের নিদর্শন এই গীর্জার হাজারো স্মৃতিকে ঘিরে উৎসবী আমেজ এখন। চলছে জোরকদমে প্রস্তুতি।
চিত্র ঋণ – সৌমেন্দু চক্রবর্তী





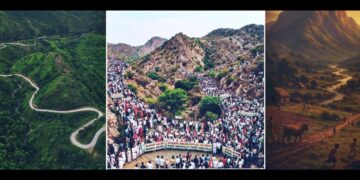








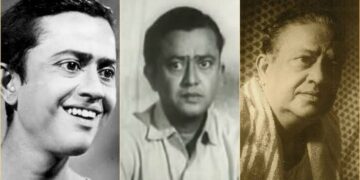




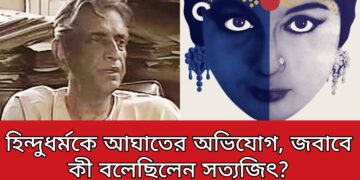
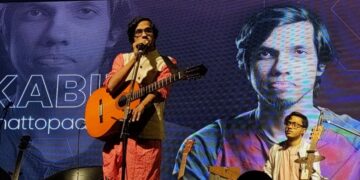



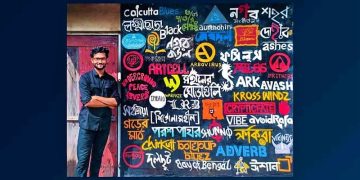






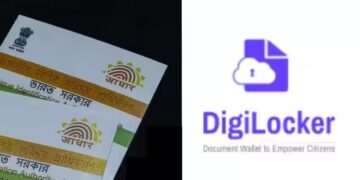










Discussion about this post