ভারতের নানারকমের গ্রামীণ লোকসংস্কৃতির এক অমূল্য ভাণ্ডার হলো আমাদের পশ্চিমবঙ্গ। নৃত্য, সঙ্গীত, হস্তশিল্প—সবক্ষেত্রেই এই ভূমি এক অপার খনি। সেই সমৃদ্ধ ধারারই এক অনন্য শাখা হল ভাদুগান, যার মূল সূত্রে জড়িয়ে আছে রাঢ়বঙ্গের বিশেষ লোকউৎসব ভাদু। পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, বীরভূম, পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিম বর্ধমানের আসানসোল থেকে ঝাড়খন্ডের রাঁচি ও হাজারিবাগ পর্যন্ত বিস্তৃত এই উৎসব। তবে ভাদ্র মাসের এই আনন্দ-উৎসবের আবহের আড়ালে লুকিয়ে রয়েছে এক হৃদয়বিদারক ইতিহাস, যাকে ঘিরেই জন্ম নিয়েছে ভাদুগান।
লোকমুখে প্রচলিত কয়েকটি কাহিনির মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল পঞ্চকোট রাজপরিবারের রাজকন্যা ভদ্রাবতীর গল্প। রাজা নীলমণি সিংদেওয়র কন্যা ভদ্রাবতী বিয়ের আগেই হারান হবু স্বামীকে—ডাকাতদলের হাতে নিহত হন বরযাত্রীরা। সেই শোক সইতে না পেরে ভদ্রাবতী স্বামীর চিতায় আত্মাহুতি দেন। প্রিয় কন্যার স্মৃতি চিরজীবী রাখতে রাজা নীলমণি সিংদেও প্রচলন করেন ভাদুগানের।
এই ভাদু উৎসব নিয়ে আরেকটি কাহিনি পাওয়া যায় বীরভূমে। সেখানে ভদ্রাবতীকে বলা হয় হেতমপুরের রাজকন্যা। তাঁর বিয়ে ঠিক হয়েছিল বর্ধমানের রাজপুত্রের সঙ্গে। কিন্তু ইলামবাজারের কাছে ডাকাতদের আক্রমণে নিহত হন রাজপুত্র। শোকে বিহ্বল ভদ্রাবতীও প্রিয়জনের সঙ্গে সহমরণে যান। আর সেই সূত্রেই ভদ্রাবতীর স্মৃতিতে প্রচলন হয় ভাদু উৎসবের।
তবে, রাঢ় বাংলার প্রত্যন্ত গ্রামের ভাদু কিন্তু কোনো রাজকুমারী নন, বরং সে নিতান্তই গ্রামের এক ছাপোষা মেয়ে, যে নিজের ভালোবাসার মানুষকে বাঁচানোর জন্য আত্মাহুতি দিয়েছিল নদীর জলে। গ্রাম বাংলায় বলা হয়, লারা গ্রামের মোড়ল এক ভাদ্রমাসে ধানখেতের আল থেকে কুড়িয়ে পান সদ্যোজাত এক শিশুকন্যাকে। নাম রাখা হয় ভদ্রাবতী, ডাকনাম ভাদু। সৌন্দর্য আর সুরে-সুরে বড় হতে থাকেন সে। গ্রামের কবিরাজের পুত্র অঞ্জনের সঙ্গে তাঁর প্রেমের কাহিনী ছড়িয়ে পড়ে রাজদরবার পর্যন্ত। প্রেমের খবর কানে আসামাত্রই অঞ্জনকে বন্দী করা হয় কারাগারে। এই ঘটনায় ভেঙে পড়ে ভাদু রাজার কাছে গান গেয়ে অঞ্জনের মুক্তির আর্তি জানান। সেই গানেই নরম হয় রাজার মন। কিন্তু, অঞ্জন মুক্তি পেলেও শর্ত অনুযায়ী ভাদু হারিয়ে যান চিরদিনের মতো। শোনা যায়, ভালোবাসার মানুষকে বাঁচাতে নদীতে ঝাঁপ দিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু তাঁর সুর বেঁচে থাকে লোকমুখে, বিস্তৃত হতে থাকে ভাদুগান।
এরকম নানা গল্প লোকগাথার মধ্য দিয়েই গ্রাম বাংলায় এখনো বেঁচে রয়েছেন ভাদু। ভাদ্র মাসজুড়ে পালিত হয় ভাদু উৎসব, আর গাওয়া হয় ভাদুগান। আর যেদিন সারা বাংলার অন্যান্য জায়গায় চলে বিশ্বকর্মা পুজো, ঠিক সেদিন আমাদের পশ্চিমের রাঢ় বঙ্গে বিশাল ধুমধামের সাথেই পালন করা হয় ভাদু উৎসবের প্রধান অনুষ্ঠানগুলি। এই উৎসবের প্রধান উপজীব্যই হলেন মেয়েরা, যারা নিজেদের পরিবারের কথা চিন্তা করে জীবনের শখ আহ্লাদ দূরে সরিয়ে রাখেন। গ্রামীণ নারীদের জীবনকথা—গৃহবধূর সুখদুঃখ, প্রেম-বিরহ, জীবনের সহজ-সরল চিত্রই ফুটে ওঠে ভাদু উৎসব ও ভাদু গানের মধ্যে দিয়ে।পাশাপাশি পৌরাণিক আখ্যানও স্থান পায় গানে—রামায়ণ-মহাভারত, রাধা-কৃষ্ণের প্রেম, কিংবা বারোমাস্যা। গানগুলি সাধারণত পাঁচালির ছন্দে পরিবেশিত হয়।
শুরুর যুগে ভাদুর কোনো মূর্তি প্রচলিত ছিল না। পরে ধীরে ধীরে মূর্তিপূজার রীতি শুরু হয়, বিশেষত বীরভূম অঞ্চলে। গ্রামভেদে নানা আচার-অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে মাসব্যাপী চলতে থাকে এই উৎসব। ভাদ্র সংক্রান্তির দিন প্রতিমা বিসর্জনের মাধ্যমে শেষ হয় রাঢ় বঙ্গের এই লোকউৎসব ভাদু।
ভাদুগান শুধু এক উৎসবের গান নয়; এটি রাঢ়বঙ্গের মানুষের আবেগ, স্মৃতি ও ইতিহাসের ধারক। ভদ্রাবতীর করুণ কাহিনী থেকে উঠে আসা এই গানের সুর আজও বহন করে চলেছে লোকজীবনের আনন্দ-বেদনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা। বাংলার লোকসংস্কৃতির গর্ব হিসেবে ভাদু আজও সমান তাৎপর্য বহন করছে.





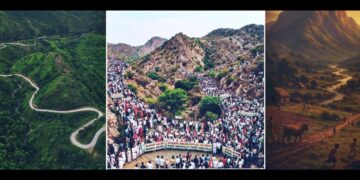








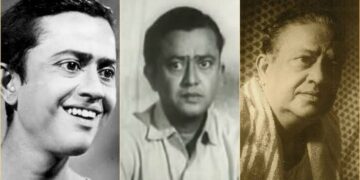




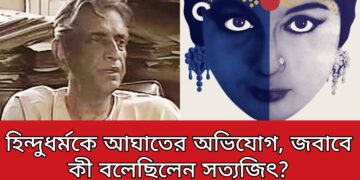
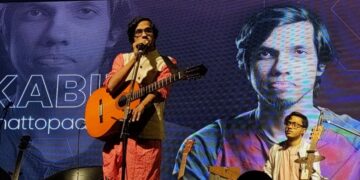



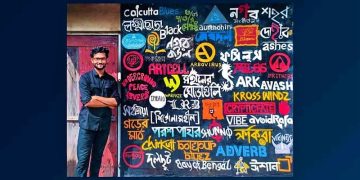






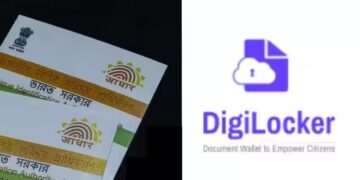










Discussion about this post